ভাতার বলে কি মাথা কিনে নেবে নাকি?তখন যৌবন কাল, শরীরে সামর্থ্য ছিলো, মনে ছিলো এক অদ্ভুত জেদ
। গ্রামের এক বাড়ির উঠোনে বসে আছে একঝাঁক অতি দরিদ্র দেহাতি মেয়ে পুরুষ বাচ্চা বুড়ো। ঘর থেকে বেরোলেন তিনি। এদের কাছে তিনি শুধুই বাবাঠাকুর। এক মহিলা ছুটে এলো, এই বাবা ঠাকুর আমার বাচ্চাটাকে আগে দেখ। পেট কেমন ফুলে গেছে।কিছু খেতে পারছে না। বৃদ্ধ ভালো করে দেখলেন। মুখ কালো হয়ে গেল তাঁর, আর কিছু না, পুষ্টির অভাব, ভিটামিনের অভাব খাদ্যের অভাব। চোখে জল এসে যায় তাঁর। বলেন ছেলেকে খাওয়াতে হবে ভালো করে। বউটি বলে শুখা সময়, খাবারের বড় অভাব গো। চাষ নাই। ওষুধ দেন তিনি। এদের জন্য অনেক কিছু করা যেত। কিন্তু আজ তিনি সম্বলহীন। বড় ভালোবাসে এরা তাঁকে। বাবাঠাকুর কে দেবতা বানিয়ে রেখেছে যেন। অথচ কি বা করতে পারেন এদের জন্য..? যেটুকু করেন এরা তাতেই খুশি। মালিন্যহীন সরল সাদা্সিধে আদিবাসী মানুষগুলি তাঁর পরম প্রিয়। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করেন তিনি। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে শহুরে দিন গুলির কথা..
তখন যৌবন কাল, শরীরে সামর্থ্য ছিলো, মনে ছিলো এক অদ্ভুত জেদ। পিতা যে জেদকে এঁড়ে বাছুরের গোঁ বলেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও বুঝে ফেলেছিলেন সারকথা। সংস্কৃত দর্শন আমাদের ভিত্তি হলেও এই কুসংস্কার আর অশিক্ষায় নিমজ্জিত জাতিকে তুলে ধরতে চাই আধুনিক শিক্ষা। একদম প্রাথমিক স্তর থেকে শেখাতে হবে মানুষকে।শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বই কোথায়? সংস্কৃতের কঠিন ব্যাকরণ এদের বোধগম্য না। শুরু করলেন সহজ বাংলার বর্ণমালা শিক্ষার বই রচনা। পাণ্ডুলিপি পড়ে বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কার সবিস্ময়ে বললেন, এসব কি করছো ঈশ্বর! বেদান্ত, দর্শন ছেড়ে শিশুপাঠ্য!! বন্ধ করো এই পন্ডশ্রম। তিনি খান্ত হননি। ১৮৫৫ সালে বেরোলো বর্ণপরিচয়। (তর্কালঙ্কার অনুধাবন করতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর বন্ধু। বুঝতে পারেননি সাদা পাতায় কালো কালিতে বিপ্লব এসেছিল বাংলা ভাষায়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই ১৫২ টি সংস্করণের ৩৫ লক্ষের বেশি বই পৌঁছে গেছিল পাঠকদের কাছে। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও বোধয় কল্পনা করেন নি, ১৫০ বছর পরেও সেই বর্ণপরিচয় কোটি কোটি বাঙালির মনে এনে দেবে এক নস্টালজিক ছোটবেলা। হাতে নিয়ে বাষ্প জমবে চোখের কোণে। এ তো বই না, এক বাঙালিয়ানার আবেগ।)
এখানেই খান্ত হবার মানুষ তিনি নন। একার ঘাড়ে তুলে নিলেন শিক্ষিত করার দায়িত্ব। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ার কাজে হাত দিলেন। খোল নলচে বদলে দিতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন গেটে, ঘুরে ঘুরে দেখতেন পাঠ দান। অধ্যাপকরা বিরক্ত হতেন। কিন্তু তিনি পরোয়া করেন নি কোনোকিছুর। কে কি ভাবলো মনে করলে কোনো কাজই করা যাবে না।তাই বেথুন এর ফিমেল স্কুলের ছাত্রী জোগাড় করতে, কলকাতার মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে তাঁর আটকায়নি। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের দায়িত্ব নিয়েই ছুটে গেছেন গ্রামে গ্রামে। একের পর এক স্কুল করেছেন। সরকার যখন সেই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নিতে অস্বীকার করেছে। তিনি সমস্ত ব্যয়ভার তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। সারাদিন স্কুল পরিদর্শন, স্কুল স্থাপনের জন্য জমিদার বা ব্যবসায়ীদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানো, সারা রাত বই লেখা। ছাপা খানা খুলে শুরু করলেন বই ব্যবসা। কলকাতার শিক্ষিত সমাজ ব্যঙ্গ করে নাম দিলো বিদ্যাবনিক। তাঁর বয়ে গেল তাতে। অর্থ চাই অর্থ। অনেক কাজ করতে হবে। মহিলা স্কুল গুলো বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না। আরো স্কুল চাই। কলকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজের কাজ শুরু হয়েছে। একটাও বন্ধ হতে দেবেন না। ভাবতে ভাবতে বিদ্যাসাগর যেন যৌবনের উন্মাদনা ফিরে পান মনে।
মনে পড়ে যায় সেই দিনটার কথা। এই কাড়মাটাঁর এর রাস্তার ধারে দেখেন চাঁদমনিকে। এই মোটা একটা কাঠ দিয়ে বেদম প্রহার করছে বরকে। তিনি বলেছিলেন, এই কী করছিস! স্বামীকে মারছিস..?
ঝংকার দিয়েছিল ফুলমণি। ভাতার বলে কি মাথা কিনে নেবে নাকি? রোজ হাঁড়িয়া পচাই খেয়ে এসে ঝঞ্ঝাট। আজ দিয়েছি বিষ ঝেড়ে। নিজের ভাত নিজে জোগাড় করি গতর খাটিয়ে। কারোর পরোয়া করিনা বাবু..।
আদিবাসী রমনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল বাংলার হাজার হাজার নারীর কথা। শত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে শুধু পরনির্ভরতার জন্য। সাবলম্বী করতে হবে তাদের। শিক্ষা দিতে হবে। একদিন বাংলার নারীকূলও এভাবেই রুখে দাঁড়াতে পারবে সমাজের বাধার বিরুদ্ধে। স্বপ্নে চোখ চকচক করে উঠেছিল তাঁর। মাথার ভেতর কিলবিল করে উঠেছিল এক জেদ। মনে পড়েছিল একাদশী, উপবাস, বঞ্চনা,অত্যাচারের জালে আবদ্ধ পর্দার আড়ালে আটকে রাখা অসহায় মুখ গুলোকে। এইসব মুখে দিতে হবে ভাষা। তারপরেই সেই বিটন সাহেবকে প্রথম মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা। নিজের উদ্যোগে ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া। বাজারে ঋণ করা। যাইহোক এতো কিছুর পরে স্কুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। সরকার অবশেষে দায়িত্ব নিয়েছে। ভেবে তৃপ্তি আসে বেশ। কিন্তু রক্ষনশীল সমাজ গুমরে উঠেছিল এই তাদের ভাষায় এই অনাচারে।
রক্ষনশীলদের সেই চাপা ক্ষোভ শতধারায় বিকশিত হল বিধবা বিবাহ আইন পাশের সময়।এখনও দেখতে পান দিনগুলো। রামমোহন মহাশয় সতীপ্রথা বধ করলেও মুক্তি হয়নি বিধবা নারীদের।শখ আহ্লাদ সাজ সজ্জা বিসর্জন তো ছিলই।অমাবস্যা পূর্ণিমা একদশীতে অসুস্থ হলে ওষুধ পথ্য দূরে থাক এক ফোঁটা জল মুখে দেবারও নিয়ম ছিল না তাদের। ছোট ছোট মেয়েগুলির সেই অনাহার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণ কেঁদে উঠত তাঁর। মনে পড়ে এক পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, “ এই কষ্ট দেখার পরেও যে সমাজ বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে,সেই সমাজকে ধিক্কার।” তৎকালীন রক্ষনশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা করেছে, নিন্দায় ভরিয়ে দিয়েছে, বড়লাটের কাছে পত্র দিয়েছে, তাকে মারার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তিনি অদম্য। শেষ পর্যন্ত পরাশর সংহিতা থেকে এনেছেন সেই শ্লোক — ❝ নষ্টে মৃতে প্রবরজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পচস্বাপতসু নারীনাং পতিরন্যে বিধয়তে ❞। যার বাংলা করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, ❝ যদি স্বামী মারা যান, সন্ন্যাস নেন, নিখোঁজ হন, সন্তান গ্রহনে অক্ষম হন, অত্যাচারী হন তবে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারে।❞ এই শ্লোকেই কাত হল রক্ষনশীল সমাজ, মানলেন বড়লাট, পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। নারীমুক্তির এক নবযুগের সূচনা হল সেদিন..
কিন্তু রক্ষনশীল সমাজ শুধু না। তথাকথিত শিক্ষিতরাও নিন্দা ব্যঙ্গে ভরালেন তাঁকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সোজাসুজিই লিখলেন, ‘বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।/ বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।।’ ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ একটি চিঠিতে পত্রলেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রীতিমতো নানা অশালীন ইঙ্গিত করলেন। রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ তাকে সহায়তা করলেন না। ১৮৮৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র এক লেখায় রামমোহন রায়ের পরে ‘দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা’ হিসেবে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষের কথা বললেও অনুচ্চারিত থাকল ঈশ্বরের নাম! বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের সূর্যমুখীকে দিয়েও বঙ্কিম লেখালেন, ❝ যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?❞ তাঁকে একঘরে করে দিলো সমাজ। মনে পড়ে আবার তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন তিনি, ❝ আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। ❞
একে একে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন সমস্ত আত্মীয়রা। আজ ভাবতে বসে খারাপ লাগে না তার। মনে হয় এইটাই তিনি চেয়েছিলেন,আদর্শের জন্য সব ত্যাগ করবো। আদর্শ আর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব না। না হননি তিনি। আজ শেষ বেলায় একটু অবাক হন, কি করে পেলেন এই মনের জোর!
তবুও শেষ বয়সে আজ তাঁর বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। সমাজ সংসারে তিনি বড় একা। সারা দেশের জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন কিন্তু তার পরিবারের মাঝেই তিনি বিচ্ছিন্ন। ভাই শম্ভুচন্দ্র এক বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাতে আর্থিক লেনদেনের খবর পেয়ে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন বলে, শম্ভু তাকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেন। তার পুত্র নারায়ন জড়িয়ে পড়ে অসামাজিক অনৈতিক কাজ কর্মে। ভীষণ কষ্ট নিয়েও তাঁকে ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর সেজ জামাইকে বসিয়েছিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষের পদে। অর্থ তছরুপ করে সে। লজ্জায় ধিক্কারে তাঁকে পদচ্যুত করলে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়। বীরসিংহ বাসীও তাঁর সাথে অন্যায় আচরন করে। তাঁকে গ্রামে একঘরে করার ডাক দেওয়া হয়। ধিক্কারে তিনি গ্রামের সঙ্গে শেষ ১২ বছর আর সম্পর্ক রাখেন নি। তবে কর্তব্য করেছেন। গ্রামে মায়ের নামে বিদ্যালয় করে দিয়েছেন। তিনি আজ একা সম্পূর্ণ একা। সমস্ত সম্পত্তি গেছে শিক্ষার প্রসারে। তার প্রেসের ভাগ নিয়ে মামলা করেছে তাঁর ভাই। মহৎ সব কাজে বেশিরভাগ মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি, বরং নিন্দা করেছে। অনেকে বিধবা বিবাহের নামে অর্থের লেনদেন করেছেন।ভাবতেই ঘৃণা হয় তাঁর।
ভাবতে ভাবতেই তাঁর মনে এলো সেই দিনটা। বিধবা বিবাহের প্রতিবাদে চারদিকে কুৎসা, বিরোধিতার মাঝে শান্তিপুরের তাতি সম্প্রদায় থেকে তাঁর কাছে এলো এক শাড়ি। আঁচলে লেখা আছে, — ❝বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,. সদরে করেছে রিপাের্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে…।❞
সুদূর গ্রামের মানুষদের তরফ থেকে তাঁর প্রতি অর্ঘ্য।চোখে জল এসে গেছিলো তাঁর। বর্ধমানের কলেরার সময় উপকৃত মুসলিম পাড়ার মানুষদের সেই ভালোবাসা আজও মনে পড়ে। আর আজকের এই সাঁওতাল পাড়ার মানুষদের বুকভরা ভালোবাসা, সহজ সরল জীবন যাত্রা বড় প্রিয় তাঁর কাছে। আজ আফসোস হয় স্ত্রী দিনময়ী কাছে থাকলে ভালো হত। কোনদিন তার প্রতি নজর দেওয়া হয় নি। বড় অভিমানে চলে গেছে সে।
শেষ বয়সে আবার কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে ফেরেন তিনি। বড় অভিমান ছিল তাঁর এই শহরের প্রতি, তাঁর পরিবারের প্রতি। লিখছেন, ❝ আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দ্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।❞ গ্রামেও ফেরা হয়নি আর তাঁর। গ্রামে ফেরার অপূর্ণ ইচ্ছে নিয়েই ১৮৯১-এর ২৯ জুলাই চিরঘুমে চলে যান বাঙালির প্রিয় ঈশ্বর…
♦️তথ্যসূত্রঃ Internet



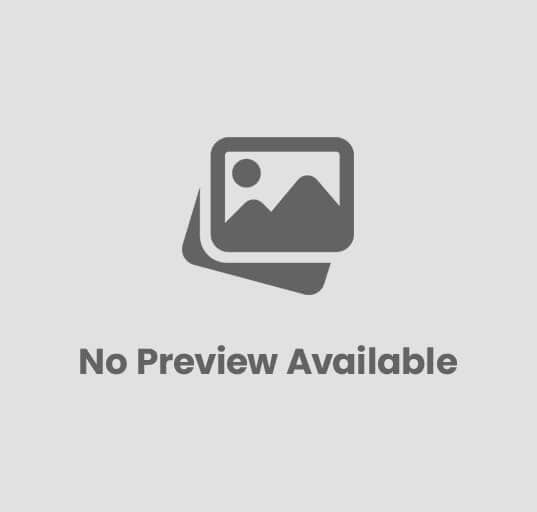







Post Comment